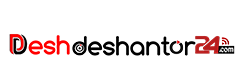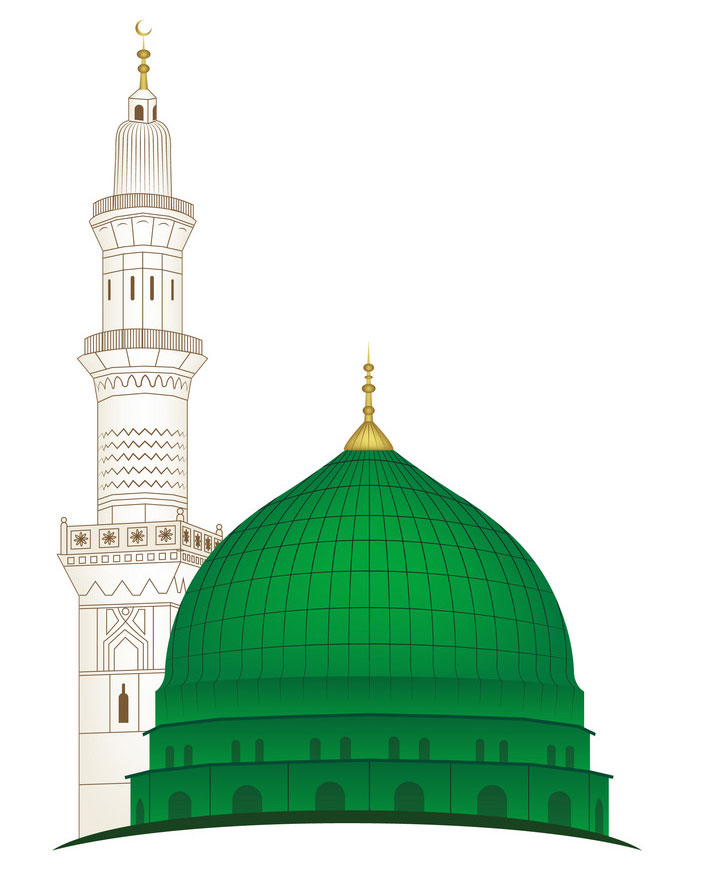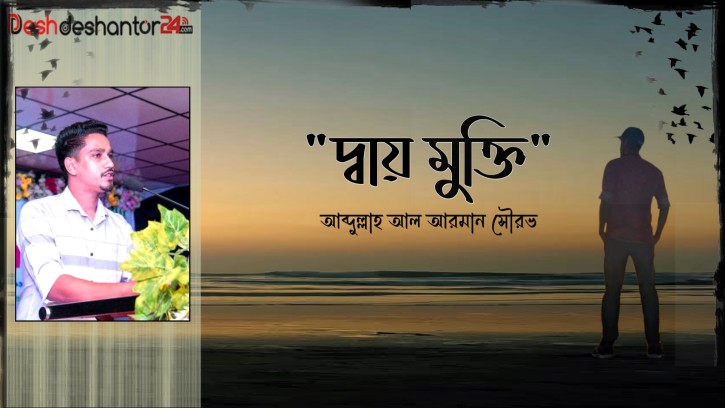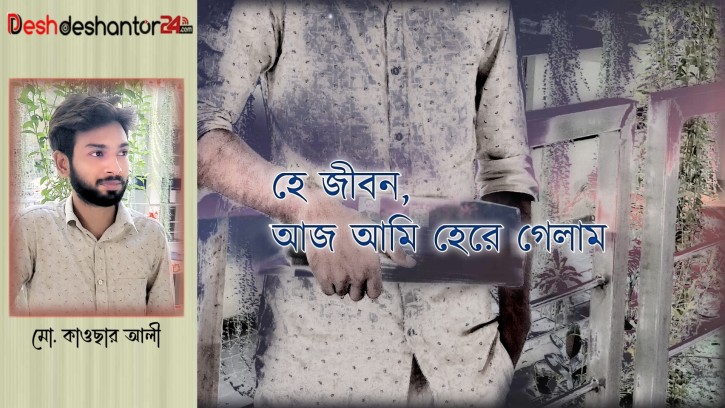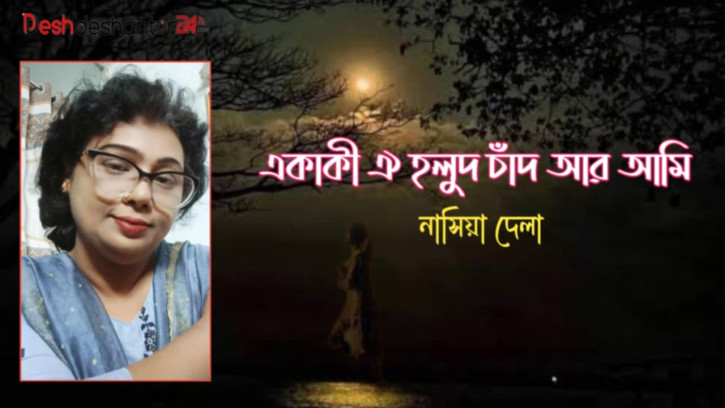ন্যায়ের আড়ালে অন্যায়: আইন ও সমতার সংকট
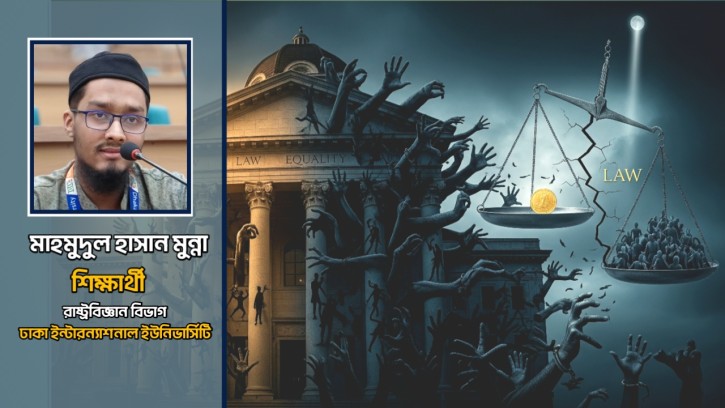
মানবসভ্যতার ইতিহাসে ন্যায়বিচারের যে মহৎ ধারণা লালিত হয়েছে তার ভিত্তি হলো — আইন সবার জন্য সমান। কিন্তু সমাজের বাস্তবতায় এ নীতি প্রায়ই বিকৃত হয়ে দেখা দেয়। কখনো আমরা দেখি, যারা কোনো ইন্টারেস্ট গ্রুপ বা স্বার্থান্বেষী মহলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ, তারা নানা সুবিধা পায়। আবার যারা সেই বলয়ের বাইরে, তাদের ওপর আইন নেমে আসে কঠোরতর রূপে। একে কি সত্যিই ন্যায় বলা যায়? নাকি এটি সেই বৈষম্য যা ন্যায়ের আড়ালে অন্যায়কে বৈধতা দেয়?
বাংলাদেশের সংবিধানও ন্যায়বিচারের এই সমতার নীতি প্রতিষ্ঠা করেছে। সংবিধানের ২৭ নম্বর অনুচ্ছেদে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে— ❝সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকারী।❞ অর্থাৎ, কোনো নাগরিকই তার সামাজিক মর্যাদা, অর্থনৈতিক অবস্থান বা রাজনৈতিক সম্পর্কের কারণে বিশেষ সুবিধা পাবে না। কিন্তু বাস্তব চিত্রে প্রায়ই দেখা যায় আইন ও শাস্তির প্রয়োগে বৈষম্য বিদ্যমান।
রাষ্ট্রবিজ্ঞানের জনক অ্যারিস্টটল তার Politics গ্রন্থে আইনকে বলেছেন "reason free from passion" (Aristotle, trans. 1998)। তার দৃষ্টিতে, আইন যদি পক্ষপাত ও আবেগমুক্ত না হয়, তবে সেটি আর আইন থাকে না, হয়ে যায় কারও প্রভাব বিস্তারের যন্ত্র। অথচ বাস্তবে প্রায়ই দেখা যায়— আইন যুক্তি নয়, সম্পর্ক ও স্বার্থের কাছে নতি স্বীকার করে।
টমাস হবস তার বিখ্যাত গ্রন্থ Leviathan (1651)-এ ব্যাখ্যা করেছেন যে রাষ্ট্র গঠনের উদ্দেশ্য হলো সকল নাগরিকের নিরাপত্তা ও সমান অধিকার নিশ্চিত করা। যদি আইন কিছু মানুষের জন্য কঠোর হয় আর অন্যদের জন্য শিথিল হয়, তবে সেই রাষ্ট্র নাগরিকদের সাথে করা সামাজিক চুক্তিকে ভঙ্গ করে। হবসের দৃষ্টিতে, এটি রাষ্ট্রের বৈধতাকেই প্রশ্নবিদ্ধ করে।
অন্যদিকে মন্টেস্কু, যিনি ক্ষমতার ভারসাম্য নিয়ে আমাদের গভীর শিক্ষা দিয়েছেন তিনি তার The Spirit of the Laws (1748) গ্রন্থে সতর্ক করে বলেছেন—
❝ There is no greater tyranny than that which is perpetrated under the shield of the law and in the name of justice.❞
অর্থাৎ, যখন আইনকে ঢাল বানিয়ে বৈষম্য করা হয়, তখন সেটিই প্রকৃত অন্যায় ও স্বৈরাচারের রূপ ধারণ করে। আজকের সমাজেও আমরা দেখতে পাই, যারা প্রভাবশালী গোষ্ঠীর সঙ্গে সম্পৃক্ত, তারা শাস্তি এড়িয়ে যায়, এমনকি যদি তারা আঘাত হানে ভাষায় বা আচরণে। বিপরীতে যারা যৌক্তিক সমালোচনা করে, তাদের পথ রুদ্ধ হয়, কণ্ঠস্বর স্তব্ধ করা হয়।
আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনায় রবার্ট ডাহল তার Democracy and Its Critics (1989) গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, গণতন্ত্র টিকে থাকতে হলে "political equality" বা রাজনৈতিক সমতা অপরিহার্য। যদি প্রতিষ্ঠানের ভেতরেই কিছু মানুষ বিশেষ সুবিধা ভোগ করে, আর বাকিদের উপর শাস্তি কঠোরভাবে প্রয়োগ করা হয়, তবে সেই প্রতিষ্ঠান গণতান্ত্রিক চেতনা হারায় এবং বৈষম্যমূলক কাঠামোয় পরিণত হয়।
এছাড়া আধুনিক রাজনৈতিক দার্শনিক জন রলস, তার বিখ্যাত গ্রন্থ A Theory of Justice (1971)-এ বলেছেন, ন্যায়বিচার হলো সামাজিক প্রতিষ্ঠানের প্রথম গুণ। তার মতে, ন্যায়বিচারের মূল নীতি হলো ন্যায্যতা (justice as fairness)। যদি সমান পরিস্থিতিতে কেউ বিশেষ সুবিধা পায়, তবে সেটি ন্যায্য নয়, বরং অন্যায়কে প্রাতিষ্ঠানিক বৈধতা দেওয়ার শামিল।
এই আলোচনাগুলো আমাদের সামনে একটি গভীর উপলব্ধি নিয়ে আসে। আইন তখনই ন্যায়বিচার হয়ে ওঠে, যখন অপরাধের গুরুত্ব অনুযায়ী বিচার হয়—অপরাধীর অবস্থান, সম্পর্ক বা প্রভাব দেখে নয়। আইন যদি কারও জন্য কোমল হয়, আর কারও জন্য নির্মম, তবে সেটি আর ন্যায় নয়; সেটি বৈষম্যের আরেক নাম।
ন্যায় শুধু আদালতের দেয়ালে ঝোলানো প্রতীক নয়, এটি সমাজের প্রতিটি স্তরে কার্যকর হওয়া উচিত। ন্যায়ের নামে যদি বৈষম্য প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে সেই ন্যায়বিচার আসলে অন্যায়েরই আরেক রূপ।
লেখক শিক্ষার্থী: মাহমুদুল হাসান মুন্না
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা ইন্টারন্যাশনা।
এএইচ